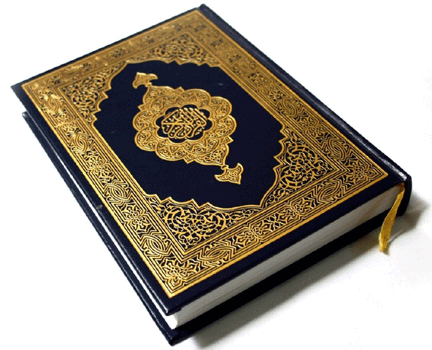
বৃহত্তর রংপুর জেলায় কুরআন চর্চার সূচনা, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
-মো: রফিকুল ইসলাম
পরোক্ষভাবে কুরআন চর্চা:
বৃহত্তর রংপুর জেলায় পবিত্র কুরআন পরোক্ষভাবে চর্চা শুরু হয় ইসলামের প্রাথমিক যুগ হতে কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে শুরু হয় ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গবিজয়ের পর হতে। তুর্কীবীর ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গ বিজয় করলে মুসলমানগণ প্রত্যক্ষভাবে বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। মুসলমানগণ মসজিদ খানকা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে ধর্ম-কর্ম পালন করেন এবং দেশবাসীর নিকট ধর্মীয় প্রচার ও ধর্মীয় বই রচনা শুরু করেন।
বখতিয়ার খিলজী বঙ্গ বিজয় করে প্রথমে অস্থায়ীভাবে রংপুরে পরবর্তীতে দেবকোটে রাজধানী স্থাপন করায় দিনাজপুরের পাশাপাশি রংপুরে ইসলামী শিক্ষার সূচনা হয়। ইতিপূর্বে পীর-দরবেশ এবং ধর্ম প্রচারকগণ অত্র এলাকায় আগমন করলেও তারা ধর্ম প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন। ইসলামী শিক্ষা এবং আল-কুরআনুল কারীম শিক্ষা ও চর্চা তখনো শুরু হয়নি। ১০/১২ বছর দেবকোটে রাজধানী থাকায় সমস্ত রংপুরে প্রশাসনিক বিভাগে অভিজাত মুসলমানগণের আবির্ভাব ঘটে। তবে একথা প্রায় দ্ব্যার্থহীন ভাষায় বলা যায় যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রংপুরে কুরআন চর্চার প্রত্যক্ষ উৎপত্তি হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দী হতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এ এলাকায় আগত সুফী, পীর-দরবেশ ও আউলিয়াগণের নির্মিত আস্তানা, খানকা, মসজিদ ও মাদরাসাসমূহে ধর্ম প্রচারের সাথে স্বল্প পরিমাণে হলেও কুরআন শরীফের চর্চা তথা পঠন-পাঠন ও মার্তৃভাষায় হৃদয়াঙ্গম চলতে থাকে। মসজিদ এবং মক্তবই বাংলার মুসলিম রাজত্বের প্রাথমিক যুগের সার্বজনীন শিক্ষার বাহন ছিল। মসজিদের বারান্দা বা মসজিদ সংলগ্ন স্থানেই মক্তব পরিচালিত হতো। তবে মুসলিম অধ্যুষিত দুই /একটি গ্রামে ধনাঢ্য মুসলমানদের অর্থায়নে ও মক্তব পরিচালিত হত। সেখানে কুরআন শরীফ পঠন ও ইসলামের প্রাথমিক কার্যাবলীসহ নামাজের প্রশিক্ষণ দেয়া হত। কুরআন শরীফ হেফজ করার জন্য পৃথক মক্তব ছিল। কোন কোন মক্তবে আরবী ব্যকরণসহ আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা দেয়া হত। এ সমস্ত মক্তবে মুসলমান ছাত্রদের সাথে হিন্দু ছাত্ররাও ফারসী ভাষা শিখত। পরবর্তীতে মক্তবের শিক্ষা পদ্ধতি দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি ধারায় কুরআন, হাদীস ও ধর্ম শিক্ষা দেয়া হত, অন্য ধারায় ফারসী, বাংলা ও অংক শিক্ষা দেয়া হত। নবাবী আমলে রংপুরে আরবী, ফারসী, বাংলা ও সংস্কৃত চারটি ভাষার প্রচলন ছিল। উচ্চ শ্রেনীর মুসলমানগণ আরবী ও ফারসী দুই ভাষাই শিক্ষাগ্রহণ করত। ধর্মীয় কারণে আরবী শিখত এবং চাকরীর জন্য ফারসী শিখত। তবে নিম্ন শ্রেনীর মুসলমানগণ ধর্মীয় করণে কিছু আরবী শিক্ষা গ্রহণ করলেও চাকরী দু®প্রাপ্য ভেবে ফারসী ভাষা শিখত না।
ধর্মীয় বই রচনা করার ধারবাহিকতায় বলা যায়, মধ্যযুগীয় কবি শাহ মুহাম্মদ সগীর তার সাহিত্যে কুরআনী মর্ম পেশ করেন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের কবি সৈয়দ সুলতান ‘ওফাতে রাসুল’ কাব্য রচনা করেন যা কুরআনী সাহিত্য চর্চা বলা যায়। তিনি ‘য়ুসুফ জলিখা’ নামক কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন যা সুরা ইউসুফের মর্মার্থ। উদাহরণ স্বরূপ উক্ত কাব্যগ্রন্থের অংশ বিশেষ নিম্নে উপস্থাপন করা হল : (সুরা ইউসুফের ৩১নং আয়াতের বঙ্গানুবাদ)
দেখিলেন্ত পরতেক কিবা এ স্বপন
এক দৃষ্টি নেহালেন্ত পাসরি আপন।।
হাতেত তুরঞ্জ ফল কাতি খরসান।
হস্ত সমে ফল কাটে মনে নাহি জ্ঞান।।
কেহ ফল কাটিতে অঙ্গুলি কাটিয়া নিল।
কিবা কর কিবা ফল এক ন জানিল।।
………………………………….
………………………………….
স্তিরি সবে বোলে এই মনুষ্য মুরতি
স্বর্গ মৈর্ত পাতালি জিনিয়া রূপ খ্যাতি।
তুলুনামূলক পর্যালোচনার জন্য আল-কুরআনুল কারীমের সুরা ইউসুফের ৩১ নং আয়াতটি এবং তার সরল বঙ্গানুবাদ নিম্নে উপস্থাপন করা হল: فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن و اعتدت لهن متكاْ و اتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما راينه اكبرنه و قطعن ايديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الاملك كريم
অর্থ: যখন সে তাদের চক্রান্ত শুনল, তখন তাদেরকে ডেকে পাঠাল এবং তাদের জন্যে একটি ভোজসভার আয়োজন করল। সে তাদের প্রত্যেককে একটি ছুরি দিয়ে বলল: ইউসুফ এদের সামনে চলে এস। যখন তারা তাকে দেখল, হতভম্ব হয়ে গেল বেং আপন হাত কেটে ফেলল। তারা বলল: কখনই নয়-এ ব্যক্তি মানব নয়। এ তো কোন মহান ফেরেশতা। শাহ মুহাম্মদ সগীরের কাব্যানুবাদ ও মূল আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, উভয় বঙ্গানুবাদের মধ্যে কোন গরমিল নেই। মূলত তার রচিত ‘য়ুসুফ জলিখা’ নামক পুরা রোমান্টিক কাব্যটি সুরা ইউসুফের পরোক্ষ বঙ্গানুবাদ বা ভাবানুবাদ।
পরবর্তীতে শাহ ইসমাইল গাজী বর্তমান বৃহত্তর রংপুর জেলায় ইসলাম প্রচারের কাজ করে ইসলামকে বিজয়ী করেন এবং সেই সাথে কুরআন চর্চায় অবদান রাখেন। বর্তমান বৃহত্তর রংপুর জেলার উত্তর পূর্বাংশে আগে উত্তর রংপুর নামে একটি জিলা ছিল। ইংরেজগণ উহার সাথে আরো কিছু অংশ যোগ করে গোয়ালপাড়া নামে একটি জেলা সৃষ্টি করেন এবং আসামের ধুবড়ী বিভাগের অন্তর্ভূক্ত করেন। সেই দুই রংপুর, আসাম, মনিপুর, জৈন্তিয়া, কাছাড়, ময়মনসিংহ এবং সিলেটের কিছু অংশ নিয়ে ১২শ শতকে শক্তিশালী কামরূপ রাজ্য ছিল। ১২০৩ সালে বখতিয়ার খিলজী এই অঞ্চলে অভিযান করে ব্যর্থ হন। আফগান সেনাপতিগণ কয়েকবার ব্যর্থ হন। সর্বপ্রথম শাহ ইসমাইল গাজী কামেশ্বরকে পরাজীত করে বশ্যতা স্বীকার করান। সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে কামরূপের ৬টি চাকলার ৩টি দখলে আসে। বাকী তিনটি সন্ধি করিয়া নামে মাত্র রক্ষা করেন। কামেশ্বরের বশ্যতা স্বীকারের ফলে তার সৈন্য ও প্রজাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেন। শাহ ইসমাইল গাজী সেই সুযোগে ইসলামের বাণী প্রচার করতে থাকেন। কুরআনী শিক্ষা প্রদান করতে থাকেন। অনেক সুফী দরবেশ ইসলামী এলাকায় প্রবেশ করে মসজিদ, ফোরকানিয়া মাদরাসা ও খানকাহ নির্মাণ করে আল কুরআনের বাণী প্রচার করতে থাকেন। রংপুরের প্রখ্যাত লেখক মোস্তফা তোফায়েল প্রায় একই ধরনের মন্তব্য করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, শাহ ইসমাইল গাজীর কারামত চাক্ষুষ অবলোকন করে রাজা কামেশ্বর এবং তার স্ত্রী বশ্যতা স্বীকার করলে তার সেনাবাহিনী এবং তার রাজ্যের তথা তৎকালীন রংপুরের অসংখ্য হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। হিন্দুদের ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে কুরআনের চর্চা হয়েছে। কেননা ইসলাম গ্রহণ করার অর্থই হল কুরআনুল কারীমসহ গোটা ইসলামী শরীয়তকে মেনে নেয়া।
প্রত্যক্ষভাবে কুরআন চর্চা:
উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা প্রত্যক্ষভাবে শুরু হয়। অজ্ঞ মুসলমানগণ যেভাবে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ত ঠিক তেমনি পীর দরবেশের মাজারে গিয়া মাথা ঠুকতো। এ ধরণের শিরক বন্ধ করা ও ধর্মীয়ভাবে সচেতন করার জন্য বাংলা ভাষায় কুরআন অনুবাদ করা হয়। কেননা কুরআন শরীফ আরবী এবং আমাদের মাতৃভাষা বাংলা হওয়ায় অনেকেই কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করত তবে কিছুই বুঝত না। দোভাষী বাংলা তথা পুঁথি সাহিত্যের ভাষায় কুরআনের তরজমা করা হত শুরুতে তথা উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে।
১৮০৮/১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে রংপুরের মটুকপুর নিবাসী আমির উদ্দীন বসুনিয়া আমপারার পুঁথি সাহিত্যের ভাষায় প্রথম প্রত্যক্ষ অনুবাদক। বাংলা ভাষায় তার আগে আর কেহ কুরআনুল কারীমের অনুবাদ করেন নাই। ভাই গিরিশ চন্দ্র সেনের কথা কেউ কেউ বললেও তা সঠিক নয়। তবে পূর্ণাঙ্গ আল-কুরআনুল কারীমের অনুবাদক হিসাবে ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন সর্বপ্রথম কুরআনের বঙ্গানুবাদ করেছেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে লক্ষ্য করলে আমির উদ্দীন বসুনিয়াই সর্বপ্রথম আল-কুরআনুল কারীমের বঙ্গানুবাদক। প্রথম পূর্ণাঙ্গ কুরআনের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৮১-১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে। অনুবাদক ব্রাক্ষধর্মাবলম্বী গিরিশ চন্দ্র সেন। আমির উদ্দীন বসুনিয়ার পর কুরআনের বঙ্গানুবাদ চর্চায় এগিয়ে আসেন কলকাতার পাটওয়ার বাগানের মির্জাপুর মহল্লার অধিবাসী আকবর আলী, ব্রিটিশ ভারতের অধিবাসী রাজেন্দ্রনাথ মিত্র, কলকাতার তারাচরণ বন্দোপাধ্যায়, টাঙ্গাইলের মাওলানা নঈমুদ্দীন, দিনাজপুরের আকবর উদ্দীন, বৃটিশ ভারতের অধিবাসী দেশীয় খ্রিস্টান শ্রী ফিলিপ বিশ্বাস।
জনাব আকবর উদ্দীনের খন্ডিত অনুবাদ ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর হতে প্রকাশিত হয়েছে। রংপুর নিবাসী মুনীর উদ্দিন আহমদ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে কুরআনুল কারীমের একখানা অনুবাদ লিখেন। তার এ অনূদিত কিতাবের নাম প্রদান করেন ‘হাফীজীল কাদেরী’।
অবশ্য আমীর উদ্দীন বসুনিয়ার আমপারার বঙ্গানুবাদখানি প্রকাশিত হওয়ার সাল নিয়ে মতামত পরিলক্ষিত হয়। অধ্যাপক আব্দুস সালামের মতে আমপারার পদ্যানুবাদটি ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে। আবার মুফাখখার হুসেইন খাঁনের মতে আমপারার কাব্যানুবাদটি ১৮৬৬ সালের পরে মুদ্রিত হয়েছে। মুফাখখার হুসেইন সাহেব হামেদ আলীর বক্তব্যকে ভিত্তি করে এমন্তব্য করেছেন। হামেদ আলী সাহেবের বক্তব্য হল ‘এই বইখানি সেকালের কোন লিথো প্রেসে মুদ্রিত হয়েছিল’। লিথো প্রেস ১৯২৩ সালের ২৯ মার্চ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গভর্নমেন্ট ড. জেম্বস রাইন্ডের তত্ত¡াবধানে কলকাতায় সর্বপ্রথম লিথোপ্রাফিক প্রেস স্থাপন করা হয়। তাই তিনি বলেন ১৮৬৬ সালের পরে ছাড়া পূর্বে মুদ্রিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, লিথো মুদ্রণ সর্বপ্রথম ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে আবিস্কৃত হয়। যেহেতু হামেদ আলীর বক্তব্যে স্থানের কথা উল্লেখ নাই। তাই কলকাতার বাইরে অন্য কোনখানে ছাপানো হতে পরে এ সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। তাছাড়া ১৮৬৬ সালের আগেই যে ছাপানো হয়েছিল এ ব্যাপারে আরো তথ্য পাওয়া যায়। যেমন কবি শেখ ফজলল করিমের ভাষায়, ‘অতি প্রাচীন পাথরে আরবী ও বাংলা হস্তাক্ষরের মত ছাপা’। এ বাক্যদ্বারা প্রাচীনত্ব ও ছাপার ধরণ উন্নত এ দুই দিকের সাদৃশ্য বুঝায়, পাথরের বøকের লিথো মুদ্রনের কথা বুঝা যায় না। সুতরাং পাথর বা কাঠ যে বøকেই হোক উন্নতমানের পাথরের মত বøকে ছাপানো হয়েছিল এটাই বুঝায়। অতএব ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ বা তার পরে ছাপানোর যুক্তি সঠিক বলে মনে হয় না।
সুতরাং স্বপ্রমাণিত হল আমীর উদ্দীন বসুনিয়ার আমপারার অনুবাদ ও প্রকাশকাল ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দ। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ৩টি কপি ছিল। ১কপি কবি শেখ ফজলল করিমের নিকট, ১কপি আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদের নিকট, ১কপি কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারের ৫০২ নং সংখ্যায় মওজুদ ছিল কিন্তু বর্তমানে তা দুষ্প্রাপ্য।
তরজমা চর্চা:
(ক) বিভিন্ন ভাষায় আল-কুরআনের অনুবাদ:
রাসুল (স.)এর জীবদ্দশাতেই কুরআনুল কারীমের অনুবাদ চর্চা শুরু হয়। বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিগণ রাসুল (সা.) এর দরবারে উপস্থিত হলে তিনি তাদের প্রত্যেকের ভাষা অনুযায়ী অনুবাদ করে বুঝাতেন। মক্কায় ইসলাম প্রচারকালে রাসুল (সা.) যখন তীব্র বাধার সম্মূখীন হচ্ছিলেন সে সময় সেখানে একজন আজমী তথা ইরানী বসবাস করতেন। তিনি দ্বিভাষী ছিলেন অর্থৎ আরবী ও ফার্সী দুই ভাষা বুঝতেন। কুরআন শুনামাত্রই নিজে বুঝার জন্য তা অবচেতনে ফার্সীতে অনুবাদ করতেন।
সপ্তম হিজরীর মুহাররম মাসে ০৬ জন ছাহাবীকে প্রতিবেশি রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানদেরকে ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত চিঠি পৌছায়ে দিয়ে তাদের ভাষায় বুঝানোর জন্য প্রেরণ করেছিলেন। মহানবী (সা.) যে দেশে যে দূত প্রেরণ করতেন সে উক্ত দেশের ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। বিভিন্ন গোত্রের ভাষা এবং বিদেশী ভাষা শিক্ষার জন্য রাসূল (সা.) সাহাবীদেরকে উৎসাহিত করতেন। এমনকি কাতিব-ই-অহি হযরত যায়দ বিন সাবিত (রা.) কে সুরিয়ানী ও হিব্রæভাষা শিক্ষার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।
আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর নিকট পত্র বাহক ছিলেন আমর ইবনে উমাইয়্যা আদ্ দ্বারমী عمرو بن امية الدرمى সাহাবী। তিনি বাদশা নাজ্জাশীকে চিঠিটি তাদের আমহারিক ভাষায় অনুবাদ করে শুনায়েছেন।
ইরানের সালমান ফার্সী (রা.) ও আফ্রিকার বিলাল (রা.) সহ কয়েকজন অনারব সাহাবী ছিলেন যারা স্বভাষার পাশাপাশি আরবী ভাষা জানতেন। তারা ছিলেন দ্বিভাষী। স্বভাষার লোকদের নিকট ইসলাম প্রচারের সময় স্বভাষায় কুরআনের অনুবাদ করতেন। পত্রের মাধ্যমে পারস্যবাসীগণ সালমান ফারসী (রা.) এর নিকট সুরা ফাতিহার অনুবাদ করার অনুরোধ জানালে রাসুল (সা.) এর অনুুমতিক্রমে তিনি ফার্সী ভাষায় তার অনুবাদ করেন। ইহাই পবিত্র কুরআনের পূর্ণাঙ্গ সুরার প্রথম অনুবাদ।
হযরত কুতায়বা (রা.) ৭১০ খ্রি./৯৪ হিজরীতে রাশিয়ার বুখারায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। পাশেই একটি মন্দির ছিল। জুমার দিনে জুমার নামাজে অংশগ্রহণকারীদেরকে দুই দিরহাম দেয়ার জন্য সেখানে ঘোষণা দেয়া হত। যারা আরবী জানতেন না আরবী না জানা পর্যন্ত ফার্সীতে নামাজ পরতেন।
(খ) বাংলা ভাষায় আল-কুরআন অনুবাদের সূচনা:
সপ্তম শতাব্দীতে ইসলাম ও আল-কুরআন বাংলাদেশে পদার্পন করে কিন্তু বাংলা ভাষায় তা অনুবাদ করা যাবে কিনা এ নিয়ে কঠিন মতানৈক্যের কারণে এবং কিছু অজ্ঞ লোকদের বিরোধিতার জন্য পারদর্শী ব্যক্তিগণ অনুবাদের কাজে হাত দেয়ার সাহস করেন নাই। তাই অনেক দেরীতে আল-কুরআনুল কারীমের অনুবাদের কাজ শুরু হয়। প্রথম দিকে পূঁথি সাহিত্যের ভাষায় কাব্যছন্দে কুরআনের বঙ্গানুবাদ চর্চা শুরু হয়। বাংলা পয়ার ছন্দে কুরআনের পূর্ণাঙ্গ কাব্যানুবাদের পথিকৃত হচ্ছেন কবি মুহাম্মদ আবদুল বারী। তিনি বর্তমান মাগুরা জেলার মুহাম্মদপুর উপজেলার হরেকৃষ্ণপুর (বর্তমানে ইসলামপুর) গ্রামের অধিবাসী। পরোক্ষভাবে ভাবানুবাদ চর্চা শুরু হয় চৌদ্দ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে। ১৪শ শতকের রোমান্টিক কবি শাহ মুহাম্মদ সগীর ‘য়ুসুফ জলিখা’ নামক কাব্যগ্রন্থে সুরা ইউসুফের ভাবানুবাদ করে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম কুরআনের অংশ বিশেষের পরোক্ষ কাব্যানুবাদ করেছেন। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চার আর কোন ইতিহাস খুজে পাওয়া যায় না। তবে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগে (১২০০-১৮০১) উনিশ শতকের শুরুতে প্রত্যক্ষভাবে সরাসরি অনুবাদ চর্চা শুরু হয়। মরহুম আমীর উদ্দীন বসুনিয়া প্রত্যক্ষ অনুবাদের পথিকৃত কিন্তু তিনি শুধু আমপারা অংশের অনুবাদ করেছেন। সম্পূর্ণ কুরআনুল কারীমের অনুবাদ তিনি করেন নাই। উনিশ শতাব্দীর শেষের দিকে কুরআনুল কারীমের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ ও তাফসীর পেশ করেন হিন্দু হতে ধর্মান্তরিত ব্রক্ষধর্মাবলম্বী ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন।
খ্রিস্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যে রংপুরের মটুকপুর নিবাসী আমীর উদ্দীন বসুনিয়া সর্বপ্রথম কুরআনুল কারীমের অংশ বিশেষের (আমপারা) সরাসরি তরজমা করেন। তিনি মুসলমানী বাংলা তথা পুথি সাহিত্যর ভাষায় ত্রিশতম পারার (আমপারা) বাংলা কাব্যানুবাদ করেন।
(গ) পদ্যানুবাদের শেষ ও গদ্যানুবাদের শুরু:
উনবিংশ শতাব্দীতে শুরু হয়ে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি হতে চতুর্থ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত আল-কুরআনুল কারীমের পদ্যানুবাদের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। চতুর্থ দশকের শেষ হতে শুরু হয় গদ্যানুবাদের প্রবণতা। তখন থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত গদ্যানুবাদের মাধ্যমেই আল-কুরআনুল কারীমের তরজমা হয়ে আসতেছে। তবে বর্তমানেও দুই/একজন শিল্প হিসেবে পদ্যানুবাদ করতেছেন।
(ঘ) অমুসলিম কর্তৃক আল-কুরআনের বঙ্গানুবাদ:
উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলমানদের সাথে সাথে হিন্দু ও খ্রিস্টানদের মধ্য হতে দুই/একজন আল-কুরআনুল কারীমের বঙ্গানুবাদ করেছেন। তবে তাদের এ মহৎ কর্মে অসৎ উদ্দেশ্যই বেশি। হিন্দুদের মধ্যে যারা আল কুরআনুল কারীমের বাংলা তরজমা করেছেন তাদের কারো উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসায়িক স্বার্থ, কারো উদ্দেশ্য ছিল নিজ ধর্মের অনুকুলে সুযোগ সুবিধামত জায়গায় অপব্যাখ্যা করা। কেউবা আল-কুরআনুল কারীম জানার ও শেখার উদ্দেশ্যে জ্ঞানতৃষ্ণা মেঠাবার জন্য তরজমা করেছেন। গিরিশ চন্দ্র সাহেব তো ব্রক্ষধর্ম প্রচারের অর্থ সংগ্রহ করার জন্য আল-কুরআনের অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন। খ্রীস্টান মিশনারীদের উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার ও খ্রিস্ট ধর্ম সমুন্নত করা। তাই তারা মাঝে মধ্যে অপব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। ইসলামের প্রতি অযথা আক্রমণ ও আঘাত হানা ছিল তাদের উদ্দেশ্য।
(ঙ) আল-কুরআন চর্চার ক্রমবিকাশ:
উনবিংশ শতাব্দীর সূচনাতে আরবী এবং ফারসী ভাষা শিক্ষার জন্য বৃহত্তর রংপুরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব খুজে পাওয়া যায় না। ১৮২৩ সালের জেনারেল কমিটি কর্তৃক পরিচালিত অনুসন্ধানে কানুনগোদের সরবরাহকৃত রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যায় যে, নবাবী আমলে বৃহত্তর রংপুরে মাত্র দুইটি ফারসী স্কুল ছিল যেখানে ফারসী ভাষা শিক্ষাদানের সাথে সাথে আরবী শিক্ষা প্রদান করা হত। ১৮৭৩ সালের স্কুল পরিদর্শকের প্রতিবেদনে জানা যায় রংপুরে ৬০টি স্বদেশী স্কুলের মধ্যে ৩৬টি মক্তব ছিল, যেখানে আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা প্রদান করা হত। তবে রংপুর জেলা কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্টের মতানুসারে স্বদেশী স্কুলে সংখ্যা ৬০০ এর চেয়ে বেশি ছিল।
১৮৮২ সালে লর্ড রিপন উইলিয়াম হান্টারের সভাপতিত্বে ২২সদস্য বিশিষ্ট একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয় যা হান্টার কমিশন নামে প্রসিদ্ধ। উক্ত কমিশনের সদস্য নবাব আব্দুল লতিফ বাংলার মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতি, ধর্মীয় শিক্ষা তথা কুরআন শিক্ষার জন্য ১৭ দফা সম্বলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করেন কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি।
স্কুল পরিদর্শকের প্রতিবেদন অনুযায়ী ৬০টি স্বদেশী স্কুলের মধ্যে ৩৬টি মক্তব হলে ৬০০টির মধ্যে ৩৬০টি বা তার চেয়েও বেশি মক্তব ছিল। এই সমস্ত মক্তবে আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা প্রদান করাই ছিল মূল লক্ষ্য। এই সমস্ত মক্তবের সকল ছেলে মেয়ে প্রথমে বিশুদ্ধ কুরআন পঠন পদ্ধতি শিখত। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান নামাজ, রোযা, কুরবানী, মিলাদ মাহফিল, বিবাহ পড়ানো প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দেয়া হতো মক্তবসমূহে। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ছিল না এই সমস্ত মক্তবে। ধনাঢ্য ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ অথবা গ্রামের সকলে মিলে এই সমস্ত কুরআন শিক্ষার প্রতিষ্ঠান প্রাণবন্ত রেখেছিল। ধর্মীয় অনুপ্রেরণাই ছিল এর মূল চালিকা শক্তি। তাই বলা যায় সরকারী অনুদান, বরাদ্দ না দেয়া সত্বেও এমনকি কুরআন চর্চা এবং ইসলামী শিক্ষা বন্ধের ষড়যন্ত্র করেও বৃটিশ সরকার রংপুরে কুরআন চর্চা বন্ধ করেত পারে নাই।
আরবী-ফারসী জানা আলিমদেরকে আখুন বলা হত। আখুনগণের কেহ কেহ ধর্মের তাগিদে বিনা পয়সায় স্বধর্মের ছেলেমেয়েদেরকে শিক্ষাদান করতেন। বহিরাগত জমিদারগণ বাড়ীতে আখুন তথা মৌলভী সাহেবদেরকে রেখে নিজ ছেলেমেয়েদের আরবী-ফারসী এবং কুরআন শরীফ শিক্ষা দিতেন। আরবী ভাষা লিখতে ও বলতে পারতেন না তবে কুরআন শরীফ দেখে পড়তে পারতেন এমন মৌলবী সাহেবগণ অল্প বেতনে মসজিদের বারান্দায় অথবা গ্রামের কারো বাড়ীর বারান্দায় ১৫/২০ জন ছেলে-মেয়েদেরকে নিয়ে কুরআন শরীফ পঠন শিক্ষা দিতেন। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে আরবী ফারসী জানা আখুন প্রায় ১০০০জন (এক হাজার) ছিল বৃহত্তর রংপুরে। তারা অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে আরবী ভাষা ও কুরআন শরীফ চর্চায় যথেষ্ঠ অবদান রেখেছেন। তাদের এই চর্চার হাত ধরেই কুরআন চর্চা সামনে অগ্রসর হতে থাকে।
১৮৭২ সালে রংপুর জেলার মুসলিম জনংখ্যা ছিল ৫৭.৯%। ১৯০১ সালে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ৬৩.১%। উক্ত প্রতিবেদন বলতেছে যে রংপুর অঞ্চল শুধু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠই ছিল না বরং মুসলিম জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অথচ রংপুরে মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা ও কুরআন চর্চার জন্য মক্তব পর্যায়ের শিক্ষা ব্যতীত মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না বললেই চলে। ভারত সরকারের ১৮৭২ সালের শিক্ষা কমিশন মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষাকে পাঁচ ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছিল। উক্ত পাঁচ ক্যাটাগরীর মধ্যে মাত্র প্রথম তিন ক্যাটাগরীর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ছিল বৃহত্তর রংপুরে। জুনিয়র ও সিনিয়র মাদরাসা বৃহত্তর রংপুরে ছিল না। প্রতিবেদনে যে জুনিয়র ও সিনিয়র মাদরাসার উল্লেখ করা হয়েছে তা গোটা ভারতবর্ষের চিত্র। রংপুর জেলা কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্টের মতানুসারে ৩৬০টি বা তার ও বেশি কুরআন চর্চার প্রতিষ্ঠান থাকলেও জুনিয়র পর্যায়ের কুরআন চর্চার প্রতিষ্ঠান ছিল মাত্র সাতটি।
আল-কুরআনের উচ্চ শিক্ষা অর্জন করতে হলে ভারতের দিল্লী, দেওবন্দ যাওয়ার কোন বিকল্প ছিল না। রংপুর অঞ্চলের অধিকাংশ মুসলমানগণ গরীব হওয়ায় প্রাইমারী লেবেলের কোরআন চর্চা ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষা অর্জনই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। আল-কুরআনের উচ্চ শিক্ষা অতি নগন্য হাতেগণা কয়েকজন ছাত্র গ্রহণ করতো। জুনিয়র এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের মাদরাসাসমূহে খুব বেশি ছাত্র ছিল না। তাই কুরআন চর্চা ও ধর্ম চর্চার প্রাইমারী লেবেলের প্রতিষ্ঠান মক্তবই রংপুরের গ্রামাঞ্চলের গরীব মুসলমানদের নিকট জনপ্রিয় ছিল। তাই বলা যায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত রংপুর অঞ্চলে কুরআনের প্রাইমারী লেবেলের চর্চা হত। অর্থাৎ বিশুদ্ধভাবে তেলাওয়াত পদ্ধতি শেখা হত। অল্প সংখ্যক ছাত্র যারা জুনিয়র ও মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত লেখাপড়া করত তারাই উর্দু বা ফারসী ভাষায় কুরআনের অনুবাদ শিখত। বাংলা তথা মাতৃভাষায় কুরআনের অনুবাদ ও বিধিনিষেধ শিক্ষা করার পদ্ধতি তখন রংপুর অঞ্চলে চালু হয়নি বললেও অত্যুক্তি হবে না।
ব্রিটিশ সরকার মাদরাসা শিক্ষা এবং কুরআন চর্চা বন্ধ করার পায়তারা করেছিল। তারা আরবী, উর্দূ তথা কুরআন হাদীসের কিতাব প্রকাশনার কোন পৃষ্ঠপোষকতা তো করেই নাই বরং সমস্যা সৃষ্টি করত। খান বাহাদুর আব্দুল মজিদ চৌধুরীর সাথে ব্রিটিশ সরকারের বিরোধ শুরু হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে মাদরাসার পুস্তক প্রকাশনার ব্যাপারে। তিনি সরকারের সমালোচনা করে বলেন, ‘মুসলমানদের সমস্ত পবিত্র গ্রন্থ আরবী, ফারসী অথবা উর্দূ ভাষায় লিখিত। মুসলমান পিতামাতা শুধু মাত্র বাংলা ভাষায় তাদের সন্তানদের শিক্ষাদান করতে চায় না, কারণ বাংলা ভাষা হিন্দু মূর্তিপুজার ধ্যান ধারণায় পরিপূর্ণ যা তাদের সন্তানদের নিজ ধর্মীয় আদর্শ থেকে বিচ্যুতি ঘটাবে। তাই সাধারণ চাহিদা মেটাবার জন্য ধনবান মুসলমানেরা নিজ খরচে মক্তব প্রতিষ্ঠা করে, যা না পায় কোন সরকারী সাহায্য, না পরিদর্শিত হয় কোন শিক্ষা অফিসার কর্তৃক। ফলে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত না হওয়ায় সে সমস্ত মক্তবের অবস্থান ও মর্যাদা যতটুকু হওয়া দরকার ততটুকু সম্ভব হয় নাই’।
(চ) গ্রন্থাকারে বঙ্গানুবাদ প্রকাশ:
বৃহত্তর রংপুরের আল-কুরআনুল কারীমের বঙ্গানুবাদকদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমপারার কাব্যানুবাদ লিখে প্রকাশ করেন রংপুর গঙ্গাচড়ার মটুকপুর নিবাসী আমীর উদ্দীন বসুনিয়া। তার অনূদিত আল-কুরআনের আমপারার বঙ্গানুবাদটি ১৮০৮/১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই বঙ্গানুবাদটি শুধু রংপুরের নয় বরং সমস্ত বাংলাদেশের মধ্যে সর্বপ্রথম বঙ্গানুবাদ। তবে পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ প্রথম প্রকাশ হয় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে। অনুবাদক ব্রক্ষ ধর্মাবলম্বী ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন। অবশ্য ড. মুজীবুর রহমান সাহেবের মতে ১৮৮৬ সালে ভাই গিরিশ চন্দ্র সেনের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদখানি প্রকাশ হয়। তিনি আল-কুরআনুল কারীমের বঙ্গানুবাদ শুরু করেন ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর এবং খন্ডাকারে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফের অনুবাদ করে প্রকাশ করা শেষ করেন ১৮৮৫ সালের ৩০ জুলাই। তিনটি ভাগে বিভক্ত করে তিনি সমস্ত আল-কুরআনুল কারীমের বঙ্গানুবাদ করেন এবং প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রত্যেক ভাগকে বারটি খন্ডে বিভক্ত করে প্রকাশ করেন। তবে শেষ ভাগে প্রত্যেক দুই খন্ড একত্রে প্রকাশ করেন। প্রথম ভাগে সুরা ফাতিহা হতে সুরা তাওবা পর্যন্ত মোট নয়টি সুরা, দ্বিতীয়ভাগে সুরা ইউনুস হতে সুরা আন-নাম্ল পর্যন্ত মোট আঠারটি সুরা, এবং তৃতীয় ভাগে সুরা কাছাছ থেকে সুরা নাছ পর্যন্ত মোট সাতাশিটি সুরা রয়েছে।
রংপুর নিবাসী খাঁন বাহাদুর তসলিমুদ্দীন আহমদ সমস্ত কুরআনুল কারীমের অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। তিনি অনুবাদ কর্মটি শুরু করেন ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে এবং শেষ করেন ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে। অবশ্য অধ্যাপক মনসূর উদ্দীন ভিন্নমত প্রকাশ করেন। তার মতে তসলিমুদ্দীন আহমদের অনুবাদ কর্মটি ১৯০১ সালে শুরু হয়ে ১৯১৩ সালে শেষ হয়। রংপুর জীবনের শুরু থেকেই তিনি বঙ্গানুবাদের কাজ শুরু করেন। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে মুন্সী রেয়াজুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত মাসিক ‘ইসলাম প্রচারক’ পত্রিকায় তার অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এটাই তার অনুবাদ কর্মের প্রথম প্রকাশ। পরবর্তীতে মাসিক ‘নবনুর’ মাসিক ‘বাসনা’ পত্রিকায় অনুবাদের বিভিন্ন অংশ প্রকাশিত হয়। তবে খন্ডাকারে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ২৯ তম পারা অর্থাৎ ‘তাবারাকাল্লাজী’। তার পরে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে আমপারার অনুবাদ, তারপর রংপুরের কাদেরীয়া প্রেস থেকে সুরা ফাতিহা ও সুরা বাকারার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৯২২ সালে ‘কোরআন’ শীর্ষক শিরোনামে সুরা ফাতিহা থেকে সুরা তাওবা পর্যন্ত ০৯টি সুরা সম্বলিত প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় খন্ডে সুরা য়ুনুস থেকে আনকাবুত পর্যন্ত ২০টি সুরা ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়। তৃতীয় খন্ডে সুরা রূম হতে নাস পর্যন্ত মোট ৮৫টি সুরা ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয়।
রংপুর জেলার গঙ্গাচরা উপজেলার শংকর গ্রামের অধিবাসী মাওলানা মুনীর উদ্দীন আহমদ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে কুরআনুল কারীমের তাফসীর লিখে প্রকাশ করেন। তার তাফসীরের নাম ‘হাফীজীল কাদেরী’। তিনি বাংলা পয়ার ত্রিপদী ছন্দে পবিত্র আল-কুরআনের কাব্য তাফসীর করেছেন। প্রথম খন্ডে সুরা ফাতিহা ও সুরা বাকারার অংশ বিশেষ রয়েছে। তার তাফসীরের ধরণ হচ্ছে প্রথমে তিনি ত‘াআউজ ও তাসমিয়াتعوذ و تسمية (اعوذ بالله من الشيطان الرجيم و بسم الله الرحمان الرحيم) আরবীতে লিখে বাংলা পয়ার ত্রিপদী ছন্দে কাব্যবঙ্গানুবাদ করেছেন। অতপর আরবী ও বাংলা উভয় ভাষায় সুরার নাম, রুকু এবং আয়াত সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। একটি করে আরবী আয়াত লিখে তার কাব্য তাফসীর করেছেন ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর থেকে হাফিজা খাতুন কর্তৃক ‘আমপারার (তরজমার) পদ্যানুবাদ’ নামে কুরআন শরীফের ত্রিশতম পারার কাব্যবঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়। মুহাম্মদ নূরুল আমিন নামে জনৈক মাওলানা কাব্যানুবাদটি করেছেন। তার বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়নি। কিন্তু দিনাজপুর হতে কাব্যানুবাদটি প্রকাশিত হওয়ায় প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুরেরই অধিবাসী হবেন তিনি। কাব্যানুবাদটির নাম ‘আমপারার (তরজমার) পদ্যানুবাদ’ কিন্তু মলাটের উপরে লিখা আছে ‘মাতৃভাষায় আমাপারা (বাংলা তরজামার পদ্যানুবাদ)’ পদ্যানুবাদটি ১৯৬৫ সালে করা হয়েছে এবং এর পৃষ্ঠা সংখ্যা হচ্ছে ২৮।
সাময়িক পত্রে কুরআন চর্চা:
বাংলা সাময়িক পত্রে কুরআনের বঙ্গানুবাদ চর্চা শুরু হয় উনিশ শতকের শেষার্ধের মাঝামাঝি অর্থাৎ সত্তুর দশক হতে। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ হতে চন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘বঙ্গমিহির’ পত্রিকায় তারাচরণ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ধারবাহিভাবে প্রকাশিত হয় এবং ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। রংপুরের তসলিমুদ্দীন আহমদ কৃত বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হতে থাকে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ হতে মুন্সী রেয়াজুদ্দীন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩) সম্পাদিত ‘ইসলাম প্রচারক’ পত্রিকায় বিক্ষিপ্তভাবে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বৃটিশ যুগে বৃহত্তর রংপুরের অনুবাদকদের বেশকিছু বঙ্গানুবাদ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হতে থাকে। নিম্নে কিছু নমুনা উল্লেখ করা হল:
(১) অনুবাদক ও তাফসীরকারক: তসলিমুদ্দীন আহমদ, সুরা বা অনুদিত আয়াত: আমপারা, আর রাহমান, আন্ নাজম, পত্রিকার নাম: ইসলাম প্রচারক, বর্ষ: সপ্তম, পত্রিকার সংখ্যা: জৈষ্ঠ্য ও তৎপরবর্তী সংখ্যাসমূহ, প্রকাশকাল: ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ।
(২) অনুবাদক ও তাফসীরকারক: তসলিমুদ্দীন আহমদ, সুরা বা অনুদিত আয়াত: লোকমান ও আল বালাদ, পত্রিকার নাম: নবনূর, বর্ষ: তৃতীয়, পত্রিকার সংখ্যা: ফাল্গুন ও চৈত্র (ধারাবাহিক), প্রকাশকাল: ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ।
(৩) অনুবাদক ও তাফসীরকারক: তসলিমুদ্দীন আহমদ, সুরা বা অনুদিত আয়াত: মারয়াম, পত্রিকার নাম: নবনূর, বর্ষ: চতুর্থ, পত্রিকার সংখ্যা: বৈশাখ, প্রকাশকাল: ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ।
(৪) অনুবাদক ও তাফসীরকারক: তসলিমুদ্দীন আহমদ, সুরা বা অনুদিত আয়াত: কাহ্ফ, পত্রিকার নাম: নবনূর, বর্ষ: চতুর্থ, পত্রিকার সংখ্যা: আশ্বিন-কার্তিক, প্রকাশকাল: ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ।
(৫) অনুবাদক ও তাফসীরকারক: তসলিমুদ্দীন আহমদ, সুরা বা অনুদিত আয়াত: কিয়ামা ও ইউসুফ, পত্রিকার নাম: ইসলাম প্রচারক, বর্ষ: অষ্টম, পত্রিকার সংখ্যা: অগ্রহায়ণ, প্রকাশকাল: ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ।
বৃটিশ শাসন পরবর্তী সময়ে সাময়িক পত্রে কুরআনুল কারীম চর্চা অব্যাহত থাকে কিন্তু এ সময়ে সরাসরি কোন সুরা বা সুরার অংশ বিশেষের অনুবাদ না করে আল-কুরআনুল কারীমের সাথে সম্পর্কীত বিষয় নিয়ে লেখালেখি বেশি হতে থাকে। নিম্নে এ সম্পর্কীত চিত্র উপস্থাপন করা হল:
(ক) গ্রন্থকার : শাহ মোহা: মুতী আহমদ আফতাবী।
গ্রন্থের নাম : ক্বেরাআতুল ক্বোরআন।
প্রকাশক : আবদুর রৌফ,রংপুর।
প্রকাশকাল : ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ।
(খ) গ্রন্থকার : মোহাম্মদ সানাউল্লাহ।
গ্রন্থের নাম : পবিত্র কোরানের আলোকে হযরত ঈসা আ: মৃত্যু সাব্যস্ত।
প্রকাশক : গ্রন্থকার নিজে দিনাজপুর হতে।
প্রকাশকাল : ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ।
(গ) গ্রন্থকার : ছদরুদ্দীন (১৯১০), বেলকা, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা (শিক্ষক)।
গ্রন্থের নাম : ছোটদের কুরআন কথা।
প্রকাশক : সোসাইটি ফর পাকিস্থান স্টাডিজ।
প্রকাশকাল : ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ।
(ঘ) গ্রন্থকার : মুহাম্মদ খোরশেদ আলী, রংপুর (উকিল)।
গ্রন্থের নাম : কুরআন পাকের সূচী।
প্রকাশক : সার্ভিস প্রেস, বগুড়া।
প্রকাশকাল : ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ।
(ঙ) গ্রন্থকার : অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক।
গ্রন্থের নাম : বিভিন্ন ভাষায় আল কুরআনের তরজমা ও তাফসীর।
প্রকাশক : ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, দিনাজপুর।
প্রকাশকাল : ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কুরআন চর্চা:
কুরআন চর্চার সর্বোত্তম জায়গা হচ্ছে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাকে আমরা মাদরাসা বলে থাকি। মক্তব, হাফেজীয়া, ফুরকানিয়া, নেজামিয়া বা কাওমী মাদরাসাসহ সকল আলীয়া মাদরাসায় কুরআন এবং হাদীসকে কেন্দ্র করে শিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে। তবে বর্তমানে আলীয়া বা কামিল মাদরাসাসমূহে কুরআন শরীফ ও হাদীসের জ্ঞান শিক্ষাদানের পাশাপাশি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে।
বৃহত্তর রংপুরের কুরআন চর্চার জন্য মাদরাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটি সুপ্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতি। ধর্মীয় ও জাতীয় প্রয়োজনে অতি প্রাচীনকাল হতে এ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মক্তব, ফুরকানিয়া মাদরাসাসমূহে ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সাথে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে। মসজিদ ভিত্তিক আর এক প্রাচীন শিক্ষা শাখা হাফেজীয়া মাদরাসায় হাজার হাজার ছাত্র কোরআন শরীফ মুখস্ত করতেছে।
ইবতেদায়ী, দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল এই সমস্ত শ্রেনীতে বিভক্ত মাদরাসাসমূহ। বাংলাদেশে তিনটি সরকারী মাদরাসা আছে তবে বৃহত্তর রংপুরে কোন সরকারী মাদরাসা নাই। এই সমস্ত মাদরাসা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সিলেবাসে পরিচালিত হচ্ছে। কোরআন, হাদীসসহ ইসলামী শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষা প্রদান করা হয় এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। নেযামিয়া ও কাওমী মাদরাসাসমূহ আল-কুরআন চর্চায় বিশেষ অবদান রাখতেছে। বেসরকারীভাবে এই সমস্ত মাদরাসা পরিচালিত হচ্ছে। আল-কুরআন হাদীস ও ফিকহ এর উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয় এ সমস্ত মাদরাসায় এবং সাধারণ শিক্ষাকে উপেক্ষা করে চলা হয়। প্রথম শ্রেণি থেকে শুরু শেষ পর্যন্ত মাদরাসায় লেখাপড়া করতে মোট সতের বছর সময় লাগে। একজন ছাত্র শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মাদরাসায় লেখাপড়া করলে আল-কুরআনুল কারীম, হাদীস, ফিক্হসহ শরীয়তের সকল বিষয়ে সে পারদর্শী হয়। বর্তমানে মাদরাসা শিক্ষার মান সাধারণ শিক্ষার সমপর্যায়ের হওয়ায় আলিম পাশ করার পর অনেক শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছে। বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল কলেজে বর্তমানে মাদরাসার ছাত্ররা লেখাপড়া করতেছে।
বৃটিশ আমলে ১৮৭৩ সালের স্কুল পরিদর্শকের প্রতিবেদনে ৬০টি স্বদেশী স্কুলের কথা বলা হলেও তৎকালীন রংপুর জেলা কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্টের ভাষ্য অনুযায়ী বুঝা যায় বাস্তব সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশি ছিল। তার মতে এ ধরণের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৬০০ এর ও বেশি। উভয় পরিসংখ্যানের তথ্যগত পার্থক্য হওয়ার কারণ হচ্ছে:
১.অধিকাংশ স্বদেশী স্কুল তথা মক্তব গ্রামে ছিল তাই পরিদর্শক দল তা হিসাব করতে পারেনাই।
২.সেই সমস্ত স্কুল সরকারী অনুদান প্রাপ্ত ছিল না বা সরকারী রেজিষ্টার্ড ছিল না তাই পরিদর্শকগণ তা হিসাবের আওতায় নিয়ে আসেন নাই।
৩.বৃটিশগণ মুসলিম বিদ্বেষী হওয়ায় ইসলাম ও মুসলমানদের অবদানকে তারা সবসময় ছোট করে উপস্থাপন করার চেষ্ঠা করেছে। তার প্রমাণ আমরা পাই রংপুর সংখ্যাগরিষ্ট মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা হওয়া সত্বেও এবং মুসলমানদের পক্ষ হতে বারবার তাকিদ প্রদান করা সত্বেও বৃটিশগণ ইসলামী শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে নাই।
৪.অবকাঠামো ব্যতীত যে সমস্ত মকতব মসজিদের বারান্দা বা ভিতরে পড়ানো হত অথবা কারো সরাইখানায় পড়ানো হত তা উল্লেখ করা হয় নাই।
পাকিস্থান আমলে আল-কুরআনুল কারীম চর্চার প্রতিষ্ঠান তথা ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চাহিদার তুলানায় অপ্রতুল ছিল। নিম্নে বিভিন্ন ক্যাটাগরীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা হল:
১. ফুরকানিয়া ও হাফিজিয়া মাদরাসা ৮৯ টি।
২. দাখিল মাদরাসা ৫৪টি।
৩. জুনিয়র হাই মাদরাসা ০৭টি।
৪. সিনিয়র মাদরাসা ৪১টি।
উপরোক্ত তথ্যে ফুরকানিয়া ও হাফিজিয়া মাদরাসার সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে ৮৯টি। সম্ভবত শুধু অনুদান প্রাপ্ত বা সরকারী রেজিস্টার্ড ফুরকানিয়া ও হাফিজিয়া মাদরাসার সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা সে সময়ে ব্যক্তিগত ও ইসলামপ্রিয় আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্ন লোকদের সহায়তায় প্রায় প্রত্যেকটি ইউনিয়নের ২/১টি হাফিজিয়া বা ফুরকানিয়া মাদরাসা গড়ে উঠেছিল। প্রত্যন্ত অঞ্চলে হওয়ায় বা দীর্ঘস্থায়ী না হওয়ায় সে সমস্ত মাদরাসা হিসাবের অন্তর্ভূক্ত করা হয় নাই বলে ধারণা করা যায়। তাছাড়া অসংখ্য মকতবে কুরআন শরীফ, রাহে নাজাত ও মিফতাহুল জান্নাত প্রভৃতি কিতাব পড়ানো হত। এ সমস্ত মকতবের সংখ্যা এই পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয় নাই।
১৯৯১ সালের (বাংলাদেশ আমলে) পরিসংখ্যান মোতাবেক বৃহত্তর রংপুরের কুরআন চর্চা প্রতিষ্ঠান বা ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুব একটা সন্তোষজনক নয়। কেননা এখনো ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় কম শুধু নয় বরং অর্ধেক এরও কম। ১৯৯১ সালে বৃহত্তর রংপুরে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল নিম্নরূপ:
১. দাখিল মাদরাসা ৫১৬টি।
২. আলিম মাদরাসা ৫১টি।
৩. ফাজিল মাদরাসা ৫৮টি।
৪. কামিল মাদরাসা ০৪টি।
৫. মসজিদ ১১,৩৩৯টি।
৬. কওমী মাদরাসা ৩২টি।
৭. হাফিজিয়া মাদরাসা ৯২১টি।
তবে আশাব্যঞ্জক বিষয় হচ্ছে দিন দিন উত্তরোত্তর ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
(তথ্য সূত্র গবেষক কর্তৃক সংরক্ষিত)
—————————————-
মো: রফিকুল ইসলাম
উপাধ্যক্ষ, নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসা
লালমনিরহাট
